ইসির চ্যালেঞ্জ ‘ভোটার উপস্থিতি’

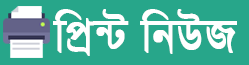
নগর খবর ডেস্ক : দুয়ারে কড়া নাড়ছে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। আগামী ৭ জানুয়ারি (রোববার) এ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। এ লক্ষ্যে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী হাবিবুল আউয়ালের নেতৃত্বাধীন নির্বাচন কমিশন সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়েছে। অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ ভোটগ্রহণ করতে কোনো কিছুর কমতি রাখছে না আউয়াল কমিশন।
তারপরও শঙ্কা, ভোটাররা নির্বাচনে ভোট দিতে আসবেন তো! ‘ভোটার উপস্থিতি’ নিশ্চিত করাই বর্তমান কমিশনের বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখছেন সংশ্লিষ্টরা। কারণ, দেশের রাজনীতিতে ‘গুরুত্বপূর্ণ’ দল বিএনপি নির্বাচন বর্জন করেছে। পাশাপাশি তাদের শরিকরাও নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে না। এ ছাড়া, বিভিন্ন কারণে ভোটের প্রতি মানুষের আগ্রহ কমে যাওয়ায় আউয়াল কমিশনকে কেন্দ্রে কেন্দ্রে ভোটার আনার চ্যালেঞ্জে পড়তে হতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।
সর্বশেষ ২০১৮ সালের একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গড়ে ৮০ শতাংশ ভোট পড়ে। নির্বাচনে ২৯৮টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা ২৫৯টিতে জয়ী হন। তাদের শরিক দলগুলো ২৯টি আসনে জয়লাভ করে। আওয়ামী লীগসহ শরিক দলগুলো মিলে গঠিত মহাজোট ওই নির্বাচনে মোট ২৮৮টি আসন পায়। ফলে টানা তৃতীয়বারের মতো সরকার গঠন করে আওয়ামী লীগ। বিএনপি নেতৃত্বাধীন জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট মাত্র সাতটি আসনে জয়ী হয়।
আইনে বলা আছে ৫ শতাংশ ভোট পড়লেও সেটা আইনানুগ নির্বাচন। তবে, গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নির্ভর করে অন্য জিনিসের ওপর। ভোটার উপস্থিতির ওপর গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নির্ভর করে না। যত শতাংশই ভোট পড়ুক না কেন সেটা আইনানুগ হবে। কিন্তু ভোট কম পড়লে সেটা নিয়ে কথা হবে
ওই সময় প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) নূরুল হুদা বলেছিলেন, ‘ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা, শান্তিপূর্ণ পরিবেশে একাদশ সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৩০ ডিসেম্বর জাতি মূলত ভোট উৎসবে মেতেছিল।’
এ ছাড়া, সর্বশেষ তিনটি সংসদ নির্বাচনের মধ্যে ২০০৮ সালের নবম সংসদ নির্বাচনে ভোটের হার ছিল সবচেয়ে বেশি, ৮৭.১৩ শতাংশ। যা বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।
একাদশ সংসদে সর্বোচ্চ উপনির্বাচন
একাদশ জাতীয় সংসদের সময়ে উপনির্বাচনে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি হয়। ওই সংসদে সর্বোচ্চ ২৬টি আসনে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সর্বশেষ গত ২৬ নভেম্বর পটুয়াখালী–১ আসনের উপনির্বাচনে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়।
উপনির্বাচন হওয়া বেশির ভাগ আসনই শূন্য হয়েছে সেখানকার সংসদ সদস্য মারা যাওয়ার কারণে। এ ছাড়া, বিএনপির সংসদ সদস্যরা পদত্যাগ করায় সংসদের আটটি আসন শূন্য হয়। ২০১৯ সালের ৩০ জানুয়ারি একাদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন বসে। ওই দিন থেকে এ সংসদের পাঁচ বছরের মেয়াদ শেষ হবে ২০২৪ সালের ২৯ জানুয়ারি।
একাদশ জাতীয় সংসদের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত ৩৬টি আসন শূন্য হওয়ায় সেখানে উপনির্বাচন আয়োজন করতে হয়েছে নির্বাচন কমিশনকে। এর মধ্যে ৩৫টিই ছিল সাধারণ আসন। আর বিএনপির ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা পদত্যাগ করায় সংরক্ষিত একটি আসনে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।
যেসব উপনির্বাচন করতে হয়েছে আউয়াল কমিশনকে
কিশোরগঞ্জ-১, বগুড়া-৬, রংপুর-৩, চট্টগ্রাম-৮, ঢাকা-১০, বাগেরহাট-৪, বগুড়া-১, যশোর-৬, পাবনা-৪, ঢাকা-৫, নওগাঁ-৬, ঢাকা-১৮, সিরাজগঞ্জ-১, লক্ষ্মীপুর-২, ঢাকা-১৪, কুমিল্লা-৫, সিলেট-৩, কুমিল্লা-৭, সিরাজগঞ্জ-৬, টাঙ্গাইল-৭, গাইবান্ধা-৫, ফরিদপুর-২, ঠাকুরগাঁও-৩, বগুড়া-৪, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২, চট্টগ্রাম-৮, ঢাকা-১৭, চট্টগ্রাম-১০, নেত্রকোণা-৪, লক্ষ্মীপুর-৩ ও পটুয়াখালী-১। এর মধ্যে বগুড়া-৬ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনে দুবার উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং ঠাকুরগাঁও-৩, বগুড়া-৪, বগুড়া-৬, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ এবং সংরক্ষিত একটি আসন মিলিয়ে সাতটি আসন বিএনপির সংসদ সদস্যদের পদত্যাগের কারণে শূন্য হয়।
ভোটের হার কমেছে সিটি নির্বাচনে
কাজী হাবিবুল আউয়াল নেতৃত্বাধীন কমিশনের আওতায় অনুষ্ঠিত হওয়া সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ভোটের হার কম পরিলক্ষিত হয়। ২০১৮ সালের তুলনায় সিটি ভোটে এ হার ৫ থেকে ২০ শতাংশের বেশি কমে। আগের নির্বাচনগুলোর সঙ্গে তুলনা করলে এ হার আরও কমবে। তবে নির্বাচন কমিশন মনে করে, স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ৫০ শতাংশ ভোটার উপস্থিতি যথেষ্ট।
আউয়াল কমিশনের অধীনে গাজীপুর, খুলনা, বরিশাল, সিলেট ও রাজশাহী সিটি নির্বাচনের ফল পর্যালোচনায় ভোটের হার কমার চিত্র পাওয়া যায়।
বর্তমান নির্বাচন কমিশন গত ২৫ মে গাজীপুর, ১২ জুন খুলনা ও বরিশাল এবং ২১ জুন সিলেট ও রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন সম্পন্ন করে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভোট পড়ে রাজশাহী সিটিতে ৫৬.২০ শতাংশ। অতীতে এ পাঁচ সিটিতে নির্বাচন ব্যালটে হলেও এবার ইভিএমে হয়। ভোট বর্জন করে বিএনপিসহ সমমনা দলগুলো। তবে, ২০১৮-সহ এসব সিটির আগের সব নির্বাচনে বিএনপি অংশগ্রহণ করে।
গাজীপুর সিটি : গত ২৫ মে অনুষ্ঠিত গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ভোট পড়ে ৪৮.৭৫ শতাংশ। গাজীপুর সিটিতে ১১ লাখ ৭৯ হাজার ৪৭৬ ভোটারের মধ্যে ভোট দেন পাঁচ লাখ ৭৫ হাজার ৫০ জন। এর মধ্যে বাতিল ভোট এক হাজার ৭৯৪টি। মোট বৈধ ভোট পাঁচ লাখ ৭৩ হাজার ২৫৬টি। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী জায়েদা খাতুন দলের মনোনীত প্রার্থী আজমত উল্লা খানকে পরাজিত করেন।
এর আগে, ২০১৮ সালে এ সিটিতে প্রথম দলীয় প্রতীকে ভোট হয়। ওই সময় ভোট পড়েছিল ৫৮ শতাংশ। ভোটে আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী জাহাঙ্গীর আলম বিএনপির হাসান সরকারকে বিপুল ভোটে পরাজিত করেন। এ সিটিতে ২০১৩ সালে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ভোটের হার ছিল আরও বেশি। ২০১৩ সালে ভোট পড়েছিল ৬৮ শতাংশ। সেবার বিএনপি সমর্থিত প্রার্থী আব্দুল মান্নানের কাছে হেরে যান আওয়ামী লীগ সমর্থিত আজমত উল্লা। পর্যালোচনা করে দেখা যায়, এ সিটিতে প্রতি নির্বাচনে গড়ে ১০ শতাংশ হারে ভোট কমেছে।
বরিশাল সিটি : গত ১২ জুন অনুষ্ঠিত বরিশাল সিটি নির্বাচনে ভোট পড়ে ৫১.৪৬ শতাংশ। এ সিটির দুই লাখ ৭৬ হাজার ২৯৭ ভোটারের মধ্যে ভোট পড়ে এক লাখ ৪১ হাজার ৭৫৬টি। বরিশাল সিটি কর্পোরেশনে ২০১৮ সালের নির্বাচনে ভোট পড়েছিল ৫৫ শতাংশেরও বেশি। এ ছাড়া, বরিশাল সিটিতে ২০১৩ সালে ৭২.১ শতাংশ, ২০০৮ সালে ভোট পড়েছিল ৮১.৯৯ শতাংশ।
খুলনা সিটি : গত ১২ জুন অনুষ্ঠিত খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ভোট পড়ে ৪৮.১৭ শতাংশ। ২০১৮ সালের নির্বাচনে খুলনা সিটিতে ভোট পড়ার হার ছিল ৬২ শতাংশের মতো। এর আগে ২০১৩ সালে ভোট পড়েছিল আরও বেশি। সেবার চার লাখ ৪০ হাজার ৫৬৬ ভোটারের মধ্যে তিন লাখ দুই হাজার ৫১৯টি ভোট পড়ে। ভোটের হার ছিল ৬৮.৭০ শতাংশ। ২০০৮ সালের নির্বাচনে এ সিটিতে ভোট পড়েছিল ৭৭.৮০ শতাংশ।
সিলেট সিটি : সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে এবার ভোট পড়ে ৪৬.৭১ শতাংশ। এ সিটিতে চার লাখ ৮৭ হাজার ৮১১ ভোটারের মধ্যে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন দুই লাখ ২৭ হাজার ৮৫৯ জন। ২০১৮ সালে ভোটের হার ছিল ৬৩ শতাংশ। এ ছাড়া, ২০১৩ সালে ভোট পড়ে ৬২ শতাংশ এবং ২০০৮ সালে ভোট পড়ে ৭৫ শতাংশ।
রাজশাহী সিটি : এবার সবচেয়ে বেশি ভোট পড়ে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে। এ সিটিতে এবার ভোট পড়ে ৫৬.২০ শতাংশ। রাজশাহী সিটিতে এবার অন্য সিটির তুলনায় ভোটের হার বেশি হলেও এ হার সিটির অন্যবারের চেয়ে কম। রাজশাহীতে ২০১৮ সালে ভোটের হার ছিল ৭৮ দশমিক ৮৬ শতাংশ। ২০১৩ সালে ভোট পড়ে ৭৬.০৯ শতাংশ এবং ২০০৮ সালে ৮১.৬১ শতাংশ।
কী অবস্থা জাতীয় সংসদ নির্বাচনগুলোতে
প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন : ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ দেশে প্রথম সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ওই সময় মোট ভোটার ছিল তিন কোটি ৫২ লাখ পাঁচ হাজার ৬৪২ জন। ভোটে এক কোটি ৯৩ লাখ ২৯ হাজার ৬৮৩ ভোটার ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। ভোট পড়ার হার ছিল ৫৫ শতাংশ।
দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন : ১৯৭৯ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। মোট ভোটার ছিল তিন কোটি ৮৩ লাখ ৬৩ হাজার ৮৫৮ জন। এর মধ্যে এক কোটি ৯৬ লাখ ৭৬ হাজার ১২৪ ভোটার ভোট দিয়েছিলেন। ভোট পড়ার হার ছিল ৫১.১২ শতাংশ।
তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন : তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১৯৮৬ সালের ৭ মে অনুষ্ঠিত হয়। ওই নির্বাচনে মোট ভোটার ছিল চার কোটি ৭৮ লাখ ৭৬ হাজার ৯৭৯ জন। এ নির্বাচনে মোট ভোট পড়েছিল দুই কোটি ৮৫ লাখ ২৬ হাজার ৬৫০টি। ৫৯.৫৮ শতাংশ ভোট কাস্ট হয়েছিল।
বরিশাল সিটি : গত ১২ জুন অনুষ্ঠিত বরিশাল সিটি নির্বাচনে ভোট পড়ে ৫১.৪৬ শতাংশ। এ সিটির দুই লাখ ৭৬ হাজার ২৯৭ ভোটারের মধ্যে ভোট পড়ে এক লাখ ৪১ হাজার ৭৫৬টি। বরিশাল সিটি কর্পোরেশনে ২০১৮ সালের নির্বাচনে ভোট পড়েছিল ৫৫ শতাংশেরও বেশি। এ ছাড়া, বরিশাল সিটিতে ২০১৩ সালে ৭২.১ শতাংশ, ২০০৮ সালে ভোট পড়েছিল ৮১.৯৯ শতাংশ।
খুলনা সিটি : গত ১২ জুন অনুষ্ঠিত খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ভোট পড়ে ৪৮.১৭ শতাংশ। ২০১৮ সালের নির্বাচনে খুলনা সিটিতে ভোট পড়ার হার ছিল ৬২ শতাংশের মতো। এর আগে ২০১৩ সালে ভোট পড়েছিল আরও বেশি। সেবার চার লাখ ৪০ হাজার ৫৬৬ ভোটারের মধ্যে তিন লাখ দুই হাজার ৫১৯টি ভোট পড়ে। ভোটের হার ছিল ৬৮.৭০ শতাংশ। ২০০৮ সালের নির্বাচনে এ সিটিতে ভোট পড়েছিল ৭৭.৮০ শতাংশ।
সিলেট সিটি : সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে এবার ভোট পড়ে ৪৬.৭১ শতাংশ। এ সিটিতে চার লাখ ৮৭ হাজার ৮১১ ভোটারের মধ্যে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন দুই লাখ ২৭ হাজার ৮৫৯ জন। ২০১৮ সালে ভোটের হার ছিল ৬৩ শতাংশ। এ ছাড়া, ২০১৩ সালে ভোট পড়ে ৬২ শতাংশ এবং ২০০৮ সালে ভোট পড়ে ৭৫ শতাংশ।
রাজশাহী সিটি : এবার সবচেয়ে বেশি ভোট পড়ে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে। এ সিটিতে এবার ভোট পড়ে ৫৬.২০ শতাংশ। রাজশাহী সিটিতে এবার অন্য সিটির তুলনায় ভোটের হার বেশি হলেও এ হার সিটির অন্যবারের চেয়ে কম। রাজশাহীতে ২০১৮ সালে ভোটের হার ছিল ৭৮ দশমিক ৮৬ শতাংশ। ২০১৩ সালে ভোট পড়ে ৭৬.০৯ শতাংশ এবং ২০০৮ সালে ৮১.৬১ শতাংশ।
কী অবস্থা জাতীয় সংসদ নির্বাচনগুলোতে
প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন : ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ দেশে প্রথম সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ওই সময় মোট ভোটার ছিল তিন কোটি ৫২ লাখ পাঁচ হাজার ৬৪২ জন। ভোটে এক কোটি ৯৩ লাখ ২৯ হাজার ৬৮৩ ভোটার ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। ভোট পড়ার হার ছিল ৫৫ শতাংশ।
দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন : ১৯৭৯ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। মোট ভোটার ছিল তিন কোটি ৮৩ লাখ ৬৩ হাজার ৮৫৮ জন। এর মধ্যে এক কোটি ৯৬ লাখ ৭৬ হাজার ১২৪ ভোটার ভোট দিয়েছিলেন। ভোট পড়ার হার ছিল ৫১.১২ শতাংশ।
তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন : তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১৯৮৬ সালের ৭ মে অনুষ্ঠিত হয়। ওই নির্বাচনে মোট ভোটার ছিল চার কোটি ৭৮ লাখ ৭৬ হাজার ৯৭৯ জন। এ নির্বাচনে মোট ভোট পড়েছিল দুই কোটি ৮৫ লাখ ২৬ হাজার ৬৫০টি। ৫৯.৫৮ শতাংশ ভোট কাস্ট হয়েছিল।
চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন : চতুর্থ সংসদ নির্বাচনে মোট ভোটার সংখ্যা ছিল চার কোটি ৯৮ লাখ ৬৩ হাজার ৮২৯। নির্বাচনে দুই কোটি ৫৮ লাখ ৩২ হাজার ৮৫৮ ভোটার ভোট দিয়েছিলেন। ৫৪.৯২ শতাংশ ভোট পড়েছিল।
পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন : ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে মোট ভোটার ছিল ছয় কোটি ২১ লাখ ৮১ হাজার ৭৪৩। এ নির্বাচনে মোট তিন কোটি ৪৪ লাখ ৭৭ হাজার ৮০৩ জন ভোট দিয়েছিলেন। ভোট পড়েছিল ৫৫. ৪৫ শতাংশ।
ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন : ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ওই নির্বাচনে মোট ভোটার ছিল পাঁচ কোটি ৬৭ লাখ দুই হাজার ৪১২। ভোট দিয়েছিলেন এক কোটি ১৭ লাখ ৭৬ হাজার ৪৮১ জন। যা মোট ভোটারের মাত্র ২৬.৫ শতাংশ।
সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন : মাত্র চার মাসের ব্যবধানে ১৯৯৬ সালের ১২ জুন সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ওই নির্বাচনে মোট ভোটার ছিল পাঁচ কোটি ৬৭ লাখ ১৬ হাজার ৯৫৩ জন। ভোট পড়েছিল ৭৪.৯৬ শতাংশ। ভোট দিয়েছিলেন চার কোটি ২৮ লাখ ৮০ হাজার ৫৭৬ জন।
অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন : ২০০১ সালের ১ অক্টোবর সাত কোটি ৪৯ লাখ ৪৬ হাজার ৩৬৪ জন ভোটার ভোট দেন। এ নির্বাচনে পাঁচ কোটি ৬১ লাখ ৮৫ হাজার ৭০৭ জন ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। ৭৫.৫৯ শতাংশ ভোট পড়েছিল।
নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন : ছবিসহ ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর আট কোটি ১০ লাখ ৮৭ হাজার তিনজনের ভোটার তালিকা প্রস্তুত করে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। ওই ভোটে সাত কোটি ছয় লাখ ৪৮ হাজার ৪৮৫ জন ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। এ নির্বাচনে গড়ে ৮৭.১৩ শতাংশ মানুষ ভোট দেন।
দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন : ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। মোট ভোটার ছিল নয় কোটি ১৯ লাখ ৬৫ হাজার ১৬৭ জন। এ নির্বাচনে ১৫৩ আসনের প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। বাকি ১৪৭টি আসনে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। মোট ৪০.০৪ শতাংশ ভোট কাস্ট হয়।
একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন : ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর ২৯৯ সংসদীয় আসনের ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। ওই সময় গাইবান্ধা-৩ আসনে এক প্রার্থীর মৃত্যু হওয়ায় সেখানে ভোট স্থগিত করা হয়। এ নির্বাচনে মোট ভোটার ছিল ১০ কোটি ৪০ লাখের বেশি। সেই হিসাবে একাদশ সংসদ নির্বাচনে ৮০ শতাংশ ভোট পড়েছিল।
দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি কেমন হতে পারে— এমন প্রশ্নে সাবেক নির্বাচন কমিশনার (ইসি) মো. রফিকুল ইসলাম ঢাকা পোস্টকে বলেন, বর্তমান কমিশনের অধীনে যে উপনির্বাচনগুলো হয়েছে, সেখান থেকে দেখেছি যে কোনোভাবেই ভোট কাস্ট ৪০ শতাংশ হয় না। এবার বিএনপি নির্বাচনে নেই, সেহেতু কোনোক্রমেই ৪০ শতাংশের বেশি ভোট পড়বে না।
৪০ শতাংশ ভোট পড়লে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন বলা যাবে কি না— এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, ‘আইনে বলা আছে ৫ শতাংশ ভোট পড়লেও সেটা আইনানুগ নির্বাচন। তবে, গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নির্ভর করে অন্য জিনিসের ওপর। ভোটার উপস্থিতির ওপর গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নির্ভর করে না। যত শতাংশই ভোট পড়ুক না কেন সেটা আইনানুগ হবে। কিন্তু ভোট কম পড়লে সেটা নিয়ে কথা হবে।’
সুষ্ঠু ভোট করার ক্ষেত্রে বর্তমান কমিশনকে কোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হচ্ছে কি না— এমন প্রশ্নে সাবেক ইসি রফিকুল ইসলাম বলেন, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ শব্দগুলো প্রচণ্ড আপেক্ষিক বিষয়। আমরা এবারই দেখছি, আওয়ামী লীগ সমর্থিত লাঙ্গলের প্রার্থী। আবার স্বতন্ত্র প্রার্থীরাও বলছেন, ‘আমি নৌকার প্রার্থী, বিজয়ী হলে শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করব’। স্বতন্ত্র প্রার্থী হলেও বেশির ভাগই কিন্তু নৌকাবিরোধী নয়, তারা ব্যক্তিবিরোধী। কাজেই এবার দলীয় কোনো লড়াই থাকছে না। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির লড়াই চলছে। জাতীয় পার্টিও আওয়ামী লীগের, বেশির ভাগ স্বতন্ত্র প্রার্থীও আওয়ামী লীগের। এক্ষেত্রে সুষ্ঠু ভোট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।
‘দল বাদ দিয়ে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির লড়াই হলে মারামারি-হানাহানি বাড়ে। এবার সংসদ নির্বাচনেও এমনটা হবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। যদি দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় তাহলে মানুষ মারা যাওয়ার রেকর্ড কম থাকে।’
বর্তমান কমিশনের প্রতি আপনার পরামর্শ কী হবে— উত্তরে তিনি বলেন, ‘নির্বাচন কমিশন, প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও বিচার বিভাগকে শুরু থেকে দৃষ্টান্তমূলক কঠোর অবস্থান নেওয়া দরকার। তারা দৃষ্টান্তমূলক কঠোর অবস্থানে যদি না যায়, নিশ্চিতভাবে পরিবেশ কন্ট্রোল (নিয়ন্ত্রণ) করা সম্ভব হবে না। শান্তিপূর্ণ নির্বাচন বিঘ্নিত হবেই।’
বর্তমান কমিশন সহিংসতা ছাড়া সুষ্ঠু নির্বাচন করতে পারবে কি না— এমন প্রশ্নে রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘এ কমিশন নিয়ে আমি কিছু বলব না। তবে নির্বাচন কমিশন, প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও বিচার বিভাগ এক হলে সুষ্ঠু ভোটগ্রহণ সম্ভব। যেটা ২০০৮ সালের পর আর কখনও হয়নি। ইতোমধ্যে দর্শকের ভূমিকা পালন করায় দুজন ওসিকে বদলি করেছে কমিশন। এতেই বোঝা যায়, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কেউ কেউ নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। এটা যদি চলতে থাকে তাহলে এ কমিশনের সুষ্ঠু ভোট করতে কষ্ট হয়ে যাবে।
‘সরকারের অধীনে থেকে যারা নির্বাচনের দায়িত্ব পালন করতে আসে তারা নির্বাচন কমিশনের আদেশ-নির্দেশগুলো খুব একটা মানতে আন্তরিক হয় না। এটা সাম্প্রতিক সময়ের কার্যক্রমেই দেখা গেছে। এ আন্তরিকতার আমূল পরিবর্তন না হলে নির্বাচন কমিশনের অসহায়ত্ব থেকেই যাবে।এটি থেকে মুক্তি পাবে না নির্বাচন কমিশন।’





